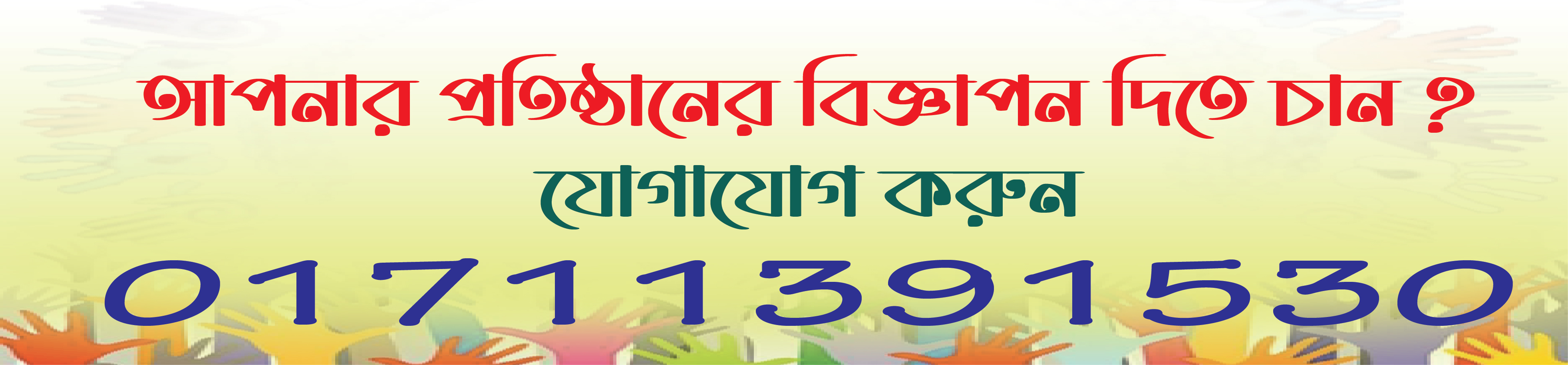ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক ভ্যালেন্টাইন দিবস
অ)
বসন্তকালের
সঙ্গে
ভালোবাসার
একটি
নিগুঢ়
সম্পর্ক
আছে,
যা
আমরা
অনেকেই
অবহিত
আছি।
এতদপ্রেক্ষাপটে
রচিত
গান
ও
কবিতার
শেষ
নেই।
এ
প্রেক্ষিতে
একটি
গানের
কথা
না
বললেই
নয়,
যেমন-
“নারীর-ও-বসন্তকালে
মুখে
মুচকী
হাসি;
পুরুষের-ও-বসন্তকালে
হাতে
মোহন
বাঁশি....................”।
মজার
ব্যাপার
হলো
যে,
আমাদের
এই
হিজল-তমাল;
শিমুল-পলাশ-ও-শাপলা-শালুকের
দেশে
ষড়ঋতু
চক্রের
আওতায়
মাধবীর
দিন
শুরু
বঙ্গাব্দের
১লা
ফাল্গুন।
আবার
সেই
দিনই
১৪
ফেব্রুয়ারী,
যা
.....
|