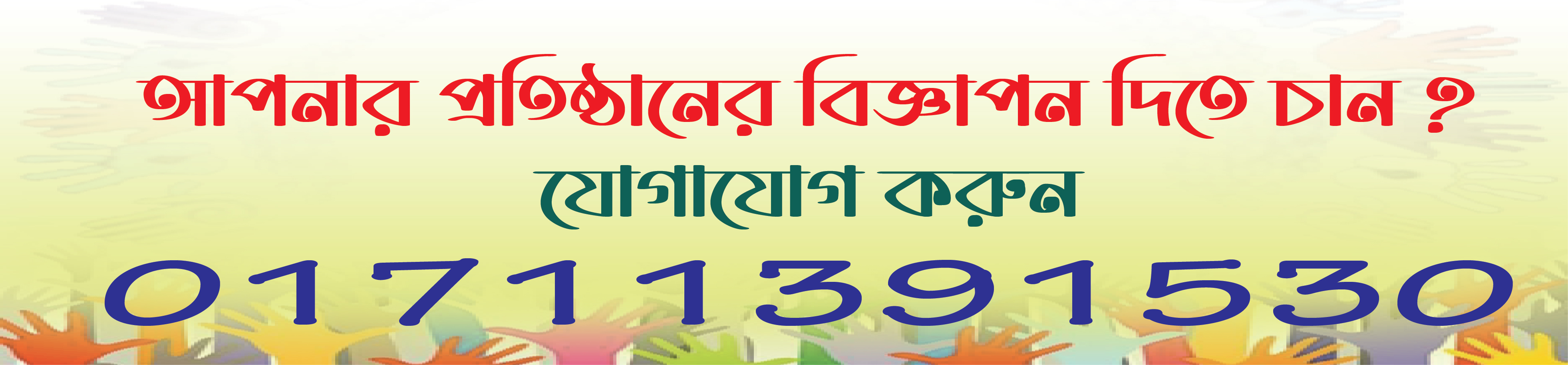| |
| বাংলা নববর্ষ উদ্ভবের ইতিহাস-কথা |
| |
|
|
|
|
|

|
|
| |
| |
 |
| |
| |
| বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিলভাঁ লেভি ফরাসি ভাষায় লেখা ‘লে নেপাল’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন যে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে স্রংসন নামে এক তিব্বতি রাজা মধ্য ও পূর্ব-ভারত জয় করেন। এবং তিনিই বাংলা সনের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নামের শেষাংশানুযায়ী সন প্রবর্তিত। এই অব্দের সঙ্গে ‘সন’ কথাটি যুক্ত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত পদ্মশ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘তিব্বতে ওই সময়ে কোনো অব্দ প্রচলনের এবং নাম রি স্রংসনের বাঙ্গালা অঞ্চল আক্রমণের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।’
বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ কখন কিভাবে প্রবর্তিত হয়েছে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। কে এই সনের প্রবর্তক তা-ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধিতসু গবেষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে ভিন্নমত ও বিতর্ক রয়েছে। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ-উপাত্তের মাধ্যমে সহসা এ বিতর্কের মীমাংসা হবে এমনও মনে হয় না। এর প্রধান কারণ এই যে বাংলা সন বাঙালি জীবনে, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ বঙ্গদেশে প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসহ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজে ব্যবহৃত হলেও আমাদের ঐতিহাসিকরা যেহেতু জনসাধারণের ইতিহাসের চেয়ে রাজবংশ, শাসক ও আধিপত্যশীল শ্রেণির ইতিহাসকেই ইতিহাস রচনার মূল প্যারাডাইম (চধৎধফরমস) নামে গ্রহণ করেন, তাই তাঁরা বাংলা সন নিয়েও খুব একটা ভাবেননি। আর এ কারণেই এখন আমরা বাংলা সনের ইতিহাস, বিশেষ করে এর প্রবর্তকের নাম নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। মধ্য যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনায় বাংলা সনের উদ্ভবের কোনো সুস্পষ্ট হদিস পাওয়া যায় না। ‘আইন-ই-আকবরী’ বা ‘আকবরনামা’য় এ সম্পর্কে পথের দিশা মেলে না। সেখানে ইলাহি সন সম্পর্কে তথ্য আছে, অন্যান্য সন সম্পর্কেও বিবরণ আছে; কিন্তু বাংলা সন সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা নেই। এ অবস্থায় আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা বাংলা সনের ঠিকুজি অনুসন্ধানে নানা উেস হাতড়ে বেড়াচ্ছেন; কিন্তু কেউই এমন মীমাংসা দিতে পারেননি যাতে বলা যেতে পারে যে এ তথ্য-প্রমাণ অকাট্য। ঐতিহাসিক ও পন্ডিতরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নানা পরোক্ষ প্রমাণ ও অনুমানের মাধ্যমে বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে চারজন সম্রাট, রাজা বা সুলতানের নাম সামনে এনেছেন। তাঁরা হলেন মোগল সম্রাট মহামতি আকবর, সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), রাজা শশাঙ্ক ও তিব্বতি রাজা স্রংসন (ইনি ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে রাজা হন এবং মধ্য ভারত ও পূর্ব ভারত জয় করেন)। সম্রাট আকবরকে যাঁরা বাংলা সনের প্রবর্তক মনে করেন, তাঁদের সংখ্যা বেশ বড়। তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল (কে পি জয়সোয়াল ১৮৮১-১৯৩৭, অক্সফোডে এমএ (ইতিহাস)), প্রতœতত্ত্ববিদ অমিতাভ ভট্টাচায, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন প্রমুখ। তাঁদের যুক্তি হলো, ১. আকবর ১৫৫৬ খ্রি. সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ৯৬৩ হিজরি ও বাংলা সনের হিসাব অনুযায়ী বাংলা সনও ৯৬৩ বঙ্গাব্দ; ২. আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে ইলাহি অব্দ সম্পর্কে লেখা আছে যে ‘আকবর বহুদিন ধরেই হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে [দিন গণনার] সমস্যাকে সহজ করে দেয়ার জন্য এক নতুন বছর ও মাস গণনাক্রম প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি হিজরি অব্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন।... আমীর ফয়জুল্লøাহ শিরাজীর প্রচেষ্টায় এই অব্দের প্রবর্তন হলো’; ৩. ‘বঙ্গাব্দ’ শব্দটি আধুনিক-এর ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়, তবে ‘সন’ ও ‘সাল’ শব্দ দুটি আরবি ও ফার্সি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলা সন বা সালের সঙ্গে কোনো হিন্দু রাজার সম্পর্ক অনুমান অবাস্তব, কোনো মুসলমান সম্রাট বা সুলতানই এর প্রবর্তক; ৪. নারদীয় পুরাণের উত্তর ভাগের একটি পুঁথির তারিখ ‘শক ১৭২৩ জ(য)বন নৃপতে শকাব্দ ১২০৮ রতœপীঠস্য নৃপতে শকাব্দ ২৯৩’; অর্থাৎ শকাব্দের ১৭২৩, যবন নৃপতির শকাব্দ (অর্থাৎ বৎসর) ১২০৮ [এবং] স্থানীয় অঞ্চলের নৃপতির শকাব্দ (বা সম্বৎসর) ২৯৩। ...আলোচ্য পুঁথিতে উক্ত যবন নৃপতির শকাব্দ বা বৎসর নিশ্চয় বাংলা অব্দের, কারণ এই বৎসরের (১২০৮) সঙ্গে ৫৯৩-৯৪ যোগ করে যে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায় (১৮০১-২), শক বৎসরটির (১৭২৩) সঙ্গে ৭৮-৭৯ যোগ করলে আমরা সেই খ্রিস্টাব্দেই (১৮০১-২) পৌঁছতে পারি। এই সমীকরণ থেকে বোঝা যায় যে ১৮০১-২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও বাঙ্গালা অব্দের উেসর সঙ্গে এক যবন নৃপতির সম্পর্কের কথা জনসাধারণের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। অমিতাভ ভট্টাচার্য যুক্তিযুক্তভাবেই অনুমান করেছেন যে মুসলমান বাদশাহ আকবরের পক্ষে এই যবন নৃপতি হওয়া খুবই সম্ভবপর (বাঙ্গালা সন : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত, পৃ. ৮০-৮৭)।
পুঁথি-গবেষক ও বিশিষ্ট পন্ডিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সন-তারিখ সম্পর্কে নানা অনুসন্ধান করেছিলেন। সে জন্য তাঁকে এ অঞ্চলের সন-তারিখ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তাঁর বিশিষ্ট গবেষণাকর্ম ‘বাংলা পুঁথির তালিকা-সমন্বয়’ (প্রথম খন্ড পৃ. ৩৭৮)-এ বলেছেন, “সুলতান হোসেন শাহের সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন চালু হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালিত্বের বিকাশে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও সুলতান হোসেন শাহের অবদান বিরাট। বিদেশাগত হলেও ইলিয়াস শাহ নিজেকে ‘বাঙালি’ বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন। তিনি ‘শাহ এ বাঙালিয়ান’ বলে নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে এই দুই সুলতানের অবদান তাই খুবই বিরাট। অতএব, তাঁদের একজন অর্থাৎ হোসেন শাহের বাংলা সন চালু করা অসম্ভব নয়।” তবে সুলতানি আমল বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় এ মত মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছেন, ‘কোন বিষয় থেকে যতীন্দ্রবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা তিনি উল্লেখ করেননি। সে জন্য একে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা আছে।’ এটা ঠিক যে কোনো কোনো পুঁথিতে বঙ্গাব্দকে ‘যবন নৃপতে শকাব্দ’ বলা হয়েছে, রামগোপাল দাসের ‘রস কল্পবল্লী’র পুঁথিতেও বঙ্গাব্দকে ‘যাবনী বৎসর’ বলা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেই মনে করা চলে না যে জনৈক মুসলমান রাজা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন এবং তিনি হোসেন শাহ।
হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, এই মতের বিপক্ষে একটি যুক্তি দেখানো যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ একটি সংবৎ প্রবর্তন করেছিলেন, তা ‘নসরত্শাহী সন’ নামে পরিচিত। বঙ্গাব্দের সঙ্গে তার দুই বছরের তফাত। ১০৮৩ নসরত্শাহী সন ও ১০৮১ বঙ্গাব্দে লেখা একটি পুঁথি পাওয়া গেছে (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুঁথির তালিকা-সমন্বয়, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৭৭)। বঙ্গাব্দ যদি হোসেন শাহের দ্বারা প্রবর্তিত হতো, তাহলে তাঁর পুত্র নতুন একটি সংবৎ প্রবর্তন করতেন কি? (সুখময় মুখোপাধ্যায়, ১৪০০ সাল, শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ, কলকাতা)। এ প্রসঙ্গে আমরা আমাদের এক লেখায় বলেছিলাম যে এটা খুব মোক্ষম যুক্তি নয়। কারণ মধ্য যুগে পিতাকে হত্যা করে পুত্রের রাজা হওয়ার নজির যখন আছে তখন পিতার প্রবর্তিত সন পরিত্যাগ করে নিজের নামে একটা সন চালু করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা হোসেন শাহের সন চালু করার প্রমাণ পাইনি।
বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিলভাঁ লেভি ফরাসি ভাষায় লেখা ‘লে নেপাল’ (দ্বিতীয় খন্ড, প্যারিস ১৯০৫) শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন যে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে স্রংসন নামে এক তিব্বতি রাজা মধ্য ও পূর্ব ভারত জয় করেন। এবং তিনিই বাংলা সনের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নামের শেষাংশানুযায়ী সন প্রবর্তিত। এই অব্দের সঙ্গে ‘সন’ কথাটি যুক্ত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত পদ্মশ্রী ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘তিব্বতে ওই সময়ে কোনো অব্দ প্রচলনের এবং নাম রি স্রংসনের বাঙ্গালা অঞ্চল আক্রমণের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।’
বঙ্গাব্দসংক্রান্ত আর একটি প্রধান মতে দাবি করা হয় যে গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্ক বাংলা সনের প্রবর্তক। সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গ্রন্থ রচনা করে এই মত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল (পহেলা বৈশাখ) বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়েছিল এবং ওই দিনই শশাঙ্ক গৌড়বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। ড. অতুল সুরসহ কেউ কেউ এ মতকে সমর্থন করেছেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘এই মতের সপক্ষে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা অন্তত ঐ সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। এর কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই, যদিও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আমাদের আছে।...৫৯৩-৯৪ থেকে হাজার বৎসরের মধ্যে এমন কোনও নথিবদ্ধ তারিখ আমাদের জানা নেই, যেটিকে নিশ্চিতভাবে বঙ্গাব্দের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। শশাঙ্কের রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত সীমানার মধ্যে তাঁর পরবর্তীকালীন এক হাজার বৎসরের মধ্যে তারিখ যুক্ত যে বিরাটসংখ্যক লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে বঙ্গাব্দ ব্যবহারের চিহ্নই নেই।’ (বাঙ্গালা সন, পৃ. ৮০, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত)
এবার আমরা সাহিত্যের দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেব। কারণ সাহিত্যে ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিধৃত থাকে। আমরা জানি যে আগে নববর্ষ শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর কবিতায় অগ্রহায়ণ বন্দনা আছে। চক্রবর্তী কবি লিখেছেন, ‘ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস;/বিফল জনম তার, নাহি যায় চাষ।’ এই কবিতাংশ থেকে কি এমন ধারণা করা চলে যে ষোড়শ শতকের আগে বাংলা সন চালু হয়নি? তখন অন্য কোনো ফসলি সন চালু ছিল, যা শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসে? এই অনুমান সত্য হলে শশাঙ্ক কর্তৃক বাংলা সন প্রবর্তনের কোনো প্রশ্নই আসে না। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় আমরা অগ্রহায়ণ নয়, বৈশাখ-বন্দনা পাই। তাতে ধারণা করা যায়, তখন বাংলা সন চালু হয়ে গেছে। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন, ‘বৈশাখে এদেশে বড় সুখের সময়।/সানা ফুলে গন্ধে মন্দ গন্ধবহ হয়।’
লেখক : মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
|
| |
|
|
|