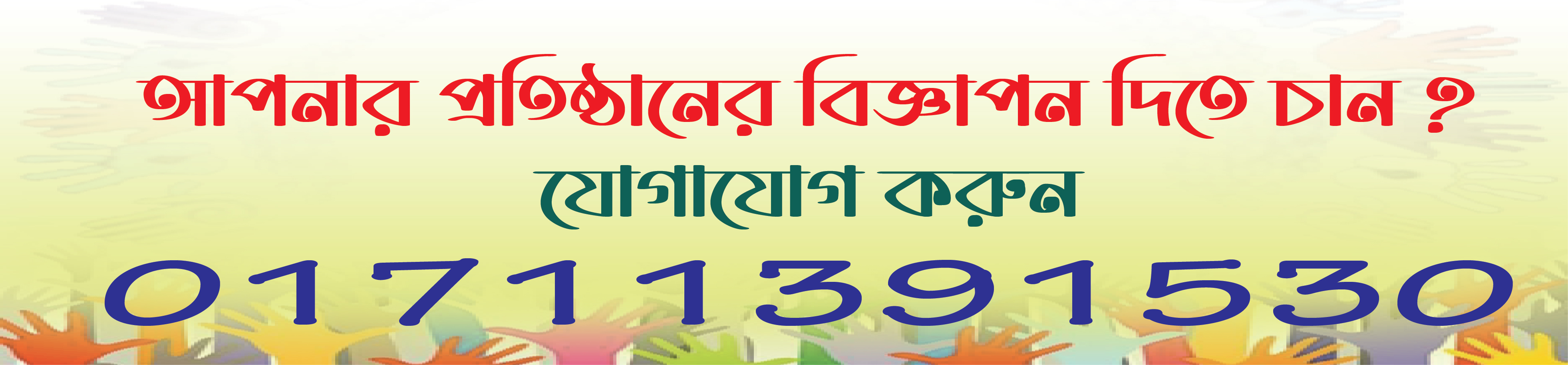| |
| চৌদ্দ এপ্রিল মানেই পহেলা বৈশাখ? |
| |
|
|
|
|
|

|
|
| |
| |
 |
| |
| |
|
বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন অর্থাৎ বাংলা নতুন সনকে সাদর সম্ভাষণ জানানো একটি বিশেষ পর্ব যার মূলে রয়েছে একটি অর্থ- জাতিগত চেতনা। অবশ্য সমাজ-রাজনীতির আবর্তন-বিবর্তনে এই পর্বটি আজ নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব শ্রেণির বাঙালির আজো জাতীয় উৎসব।
বাঙালির জীবনে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন করেছিল একমাত্র এই ‘বাংলা নববর্ষ’। ধর্মীয় পার্থক্য বাঙালি জাতিকে যেভাবেই হোক, খানিকটা বিভক্ত করেছে। একই দেশের দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাঙালিরা বিভক্ত নামে, সম্বোধনে, আদব-কায়দায়, আহার-পানীয়তে, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং আরো নানাভাবে। কিন্তু জীবনচর্চাতে তাদের পার্থক্য নেই। এই জীবনচর্চাটিই মূল। বাঙালি মুসলিমদের সঙ্গে অন্য দেশীয় মুসলিমদের ধর্ম ও ব্যক্তিনামের সাদৃশ্য থাকলেও জীবনচর্চায় সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি মুসলিমদের ধর্ম ও ব্যক্তিনামের মিল না থাকলেও জীবনচর্চায় তারা এক। এখানেই সংস্কৃতির প্রাণসুতো বিদ্যমান। বাঙালি বৌদ্ধ বা বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যেও ধর্ম ও ব্যক্তিনামের পার্থক্য দেখা যাবে। কিন্তু জীবনচর্চায় তারা এক। এই অভিন্নত্বই মহামূল্যবান। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ দুটি স্বাধীন দেশ ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথক রাষ্ট্রীয সত্তায় বাঙালিরা নিজেদের অজান্তেই পরস্পর থেকে খানিকটা দূরে সরে আসে। ১৯৫২ সালে অবাঙালিদের গ্রাস থেকে বাংলা ভাষাতে মুক্ত করার আন্দোলন অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, তার ধারাবাহিকতায় গর্বিত হয় সমগ্র বাঙালি জাতি। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি দিবসটি একান্তভাবে এবং সরকারিভাবে বাংলাদেশের বাঙালিদের। আজ অবশ্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কারণে একুশে ফেব্রুয়ারির বৈশ্বিক পরিচিতি মিলেছে। তার পরও একুশে ফেব্রুয়ারির আবেদন ও চেতনা বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে যেমন, অন্য বাঙালিদের কাছে তেমন নয়, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কাছেও নয়। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন: পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ হবে ‘বাংলাদেশ’; ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তা হিসেবে ‘বাঙালি’র স্বীকৃতি; পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় ‘বাঙালি জাতীয়তা’কে বদল করে ‘বাংলাদেশি জাতীয়তা’ করা ইত্যাদি বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে যেমন সংগ্রামের ও স্মরণযোগ্য ইতিহাস, ভারতীয় বাঙালিদের কাছে তেমনটি নয়। অন্য দিকে, ১৯৯২-’৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ‘বঙ্গ’ নাকি ‘বাংলা’ নাকি ‘গৌড়’ রাখা হবে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছেছিল। পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকা, সভা-সেমিনার, রাজনৈতিক মঞ্চ এমন কি পার্লামেন্টে প্রস্তাব ও তর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল সে সময়। এই বিতর্কে তৎকালে জড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিজনই; দেখা গেছে বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে এ আলোচনা মোটেও আগ্রহব্যঞ্জক ছিল না, কেউ কেউ এর সামান্য খবর রেখেছে মাত্র। রাষ্ট্রীয় এই চেতনাগত পার্থক্য জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে না, হলফ করে এ কথা বলা যায় না।
উচ্চারিত ভাষাভঙ্গি থেকে শুরু করে ব্যবহৃত শব্দ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বাক্য গঠনগত মৌল পার্থক্য বাংলাদেশের বাঙালি ও ভারতীয় বাঙালিদের পৃথক করেছে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভাষাতেও এই পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। দৈনিক ‘আনন্দবাজার’, ‘বর্তমান’, ‘আজকাল’ বা ‘সংবাদ প্রতিদিন’ নামের সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনের ঢঙ্ এবং সংবাদের ভাষা অবশ্যই পৃথক ঢাকার পত্রিকা দৈনিক ‘কালের কণ্ঠ’, ‘সংবাদ’, ‘ইত্তেফাক’, ‘জনকণ্ঠ’ ইত্যাদি থেকে। দৈনিক ‘কালের কণ্ঠে’র নিয়মিত একজন পাঠকের সংবাদপঠন গতি এ কারণেই ব্যাহত হতে বাধ্য ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ পাঠ করার সময়Ñ যদিও উভয় পত্রিকার ভাষাই বাংলা এবং ভাষারীতি চলিত। পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত ‘আধিকারিক’ বা ‘নিগম’ শব্দের সঙ্গে ‘অফিসার’ / ‘কর্মকর্তা’ বা ‘কর্পোরেশন’ ব্যবহারকারী বাংলাদেশের বাঙালিজন পরিচিত নন। অন্যদিকে ‘সড়কদ্বীপ’ শব্দটি শুনে যে কোনো ভারতীয় বাঙালি চমকে উঠতে পারেন। তাকে কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে, এটা তাদের দেশের ‘ট্রাফিক আইল্যান্ড’। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ‘মরিচ’কে ‘লংকা’ বলতেই অভ্যস্ত। রান্নার ‘চুলা’কে তারা ‘উনুন’ বলে থাকেন। এ পার্থক্যগুলো ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার ওপর হিন্দি ভাষার প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অন্য দিকে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার ওপর আরবি-পারসি ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট। বাংলাদেশের কোনো লেখায় ঈশ্বর দাস সকাল সকাল ‘গোশল’-এর পর ‘নাস্তা’ সেরে এক গ্লাস ‘পানি’ পান করেন। পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখায় তেমনি আবদুর রহমান ‘স্নান’ শেষে সকালের ‘জলখাবার’ সেরে এক গ্লাস ‘জল’ পান করেন। ‘জল’ ও ‘পানি’ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাঙালিরা স্পষ্ট বিভক্ত। বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল এবং এখনো অনেকের মধ্যে আছে যে, ‘পানি’ হলো মুসলমানি শব্দ অর্থাৎ আরবি বা পারসি। তাই বাংলাদেশের মুসলিম পরিবার ও সমাজে ‘পানি’ ব্যবহারের প্রচলন হয়। একই দেশ ও সমাজভুক্ত বলে বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে সে ধারাতেই ‘জল’ ব্যবহার এখন বেশ কমে গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের হিন্দুরাতো বটেই, অনেক এলাকাতেও হিন্দুদের ঘরে ‘পানি’ ব্যবহার হয়। পশ্চিমবঙ্গে ‘পানি’ ব্যবহার করে অবাঙালিরা; মুসলিমরাও ‘জল’ বলায় অভ্যস্ত। ‘পানি’ মুসলমানি শব্দÑ এ ধারণাটি সত্য নয়। তার প্রমাণ বাঙালির প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থগুলো। সে সব গ্রন্থে প্রয়োজন অনুসারে ‘পানি’ ও ‘জল’ উভয় শব্দের ব্যবহার আছে। আসলে ‘পানি’ হলো হিন্দি শব্দ যা মূলত সংস্কৃত ‘পান’ থেকে এসেছে। সংস্কৃতের ‘পানীয়’ই হলো হিন্দি ‘পানি’। আর ‘জল’ সংস্কৃত শব্দ। অর্থাৎ দুটোরই মূল সংস্কৃত। কিন্তু ‘জল’ ও ‘পানি’র ব্যবহার নিয়ে বাঙালিদের অ™ভুত রকমের ছুঁৎমার্গ দেখা যায়! অথচ মজার ব্যাপার, যারা সচেতনভাবে ‘জল’ ব্যবহার করে তারা প্রাত্যহিক জীবনে কিন্তু ‘পানিফল’ বা ‘পান্তা’ (পানি+তা) খেয়ে বা বলে থাকে। আবার যারা ‘পানি’ ছাড়া অন্য কিছু বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে, তারাও কিন্তু ছবি আঁকার সময় ‘জলরং’ ব্যবহার করে; ‘জলবায়ু’র পরিবর্তনে হঠাৎ ‘জলোচ্ছ্বাস’ এলে ভয় পেতেই হয়; মন্দ কিছু তারা ‘জলাঞ্জলি’ দিয়ে থাকে; ‘জলছাদ’ ফেটে গেলে তাদের ঘরে পানি পড়ে! অর্থাৎ ‘জল’ ও ‘পানি’ শব্দের ব্যবহার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ও বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে পার্থক্যরেখা টানা গেলেও ‘পানিফল’, ‘পান্তা’, ‘জলছাদ’, ‘জলোচ্ছ্বাস’, ‘জলবায়ু’, ‘জলরং’, ‘জলকামান’, ‘জলাঞ্জলি’, ‘জলাশয়’ ইত্যাদি বহু শব্দ দিয়ে তারা মিশে গেছে একে অপরের সঙ্গে। এখানেই সংস্কৃতির প্রাণসুতোটি এক ও অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ‘শ্রী’ নূরুল হাসান কিন্তু বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ‘জনাব’ দিলীপ বড়–য়া। ‘শ্রী’ এবং ‘জনাব’ ব্যবহারের এই রীতিটিও কিন্তু লক্ষ্যযোগ্য।
অনেকে এই বিষয়গুলোকে ‘মামুলি ধরনের’ বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন কিংবা সংস্কৃতি বিচারে এগুলোকে উপরিকাঠামোগত পার্থক্য বলে বিবেচনায় আনতে অপারগতাও প্রকাশ করতে চাইতে পারেন। কিন্তু জীবনপ্রয়াসে অঙ্গীভূত, রাষ্ট্রীয় চেতনায় আত্তীকৃত (যে রাষ্ট্র বা সরকারব্যবস্থা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত), সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাপিতজীবনে সংযুক্ত যে উপাদানগুলি একান্ত সহযোগী বা অবশ্য প্রয়োজনীয়Ñ তাকে যদি ‘সংস্কৃতি’ বলে আমরা সংজ্ঞায়িত করে থাকি, তাহলে গুরুত্বের নিরিখে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ নিতান্তই অপ্রধানÑ একথাও বলার দুঃসাহস আমাদের নেই। কেননা ইংরেজি ‘কালচার’ আর বাংলায় যাকে আমরা ‘সংস্কৃতি’ বলে থাকি, সেখানে ‘চর্চা’র প্রসঙ্গটি প্রধান বিবেচ্য। মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী বলেই সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কারকে তারা যেমন সহজেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারে না, ঠিক তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় প্রভাবকে এড়িয়ে সমাজ বিকশিত হয় না। কারণ সংস্কৃতি হলো মানবজীবনের অলিখিত ইতিহাস, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে যুক্ত। যদিও সমাজে সংস্কৃতি নির্ভরতা লক্ষ করা যায়, তথাপি সমাজই সংস্কৃতির ওপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বিস্তার করে তাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ সমাজের আন্তরকাঠামোজাত গতিশীলতাই একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধরন নির্ণয়ের মৌল অবলম্বন। তাই জাতিগত মূল পরিচয়টি সংস্কৃতিতেই ধারণ করা থাকে। সমাজকাঠামোর ওপর সমকালীন রাজনীতির প্রভাবকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তবে রাজনীতি ধীরে ধীরে সমাজকে বদলে দিতে পারে: সৎ রাজনীতি সমাজকে ভালোভাবে বদলায়, প্রগতিমুখী করে; অপরাজনীতি সমাজকে বদলায় কি¤ভূতকিমাকার করে। সমাজের বাঁক বা বদলরূপেও এখানে অন্তঃসলীলার মতো প্রবাহিত থাকে সংস্কৃতি।
আজ বাঙালি ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত, উপরন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে খ-িত। অনেকে আবার নির্বাসিত জীবিকার প্রয়োজনে এই ব্যস্ত পৃথিবীর কোনো প্রান্তে। সমাজ, রাজনীতি ও কালের প্রবাহে বাঙালির দেহ আজ খ--বিখ-। এই খ-িতাবস্থা দূরত্বের সৃষ্টি করছে। একে একদেহ করা আজ আর সম্ভবপর নয়। এ দূরত্ব বরং স্পষ্টতর হয়ে উঠছে দিনকে দিন। তাই যারা আজো ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ অভিধাটি ব্যবহার করছে, তাদের আবেগ থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে বস্তুগত বাস্তবতা নেই। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ বাঙালির খ-িত দেহে যে শোণিত প্রবাহিত তার বর্ণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। এই অভিন্নতাই বাঙালিকে পৃথক ও স্বতন্ত্র রেখেছে পৃথিবীর অন্য জাতিগুলো থেকে। বিশ্বের প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের সুর তাই আজো এক তন্ত্রীতে ধ্বনিত।
এই অভিন্ন রাগিণীর সুর-মূর্ছনায় আমরা বছরে অন্তত একদিন পরস্পরের খুব সন্নিকটে চলে আসতাম। আরো কিছু দিবস ছিলÑ যেমন, চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো আজ খ- খ-ভাবে পালিত হলেও সমষ্টিগতভাবে আমাদের নাগালের প্রায় বাইরে। এই কিছু দিন আগেও ধর্মীয় বা দৈশিক সব সংস্কার নিষেধের ঊর্ধ্বে সমগ্র বাঙালি জাতি অখ-িতভাবে মেতে উঠতাম একটিমাত্র জাতীয় উৎসবেÑ ‘বাংলা নববর্ষে’। কিন্তু আজ আর তা হয় না। বাঙালিরা আজ বিশ্ব জুড়ে সত্যি দ্বিধা বিভক্তÑ এই পহেলা বৈশাখের দিনেও। ফসল ফলানো ও খাজনা আদায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চান্দ্র বছর হিজরির পাশাপাশি মুসলিম সম্রাট আকবরের সময় সৌর বৎসর হিসেবে ‘ফসলি সন’ বা ‘বাংলা সন’ প্রবর্তিত হয়। মুসলিম সম্রাট প্রবর্তিত হলেও বাঙালি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষেই এই সনকে আপন সন হিসেবে গ্রহণ করে। ‘হাল’ ও ‘খাতা’ এ দুটি আরবি শব্দকে একীভূত করে বাঙালিজন আরম্ভ করে ‘শুভ হালখাতা’র পালা। এ সব ক্ষেত্রে তারা ভাবেনি ভারতভূমিতে আরবি ভাষায় উৎসবের নামকরণ হবে কেন? যে নামেই হোক, উৎসবটাকে তারা আপন করে নিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে সমাজ ও রাজনীতির অনিবার্য অভিঘাত ও তার প্রভাবে বাংলা সন ও তার আনুষ্ঠানিকতায় পাকিস্তান আমলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লেবেল সাঁটার অপচেষ্টা চলে। বলা হয়, এটা হিন্দুদের অনুষ্ঠান! সাধারণ মুসলিমরা এই ভাষ্যকেই সত্য ভেবেছে। তাই এতে ক্ষতিও হয়েছে অনেক। তবে এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত সাধনার কাছে।
অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে সম্পন্ন হয় ‘পঞ্জিকা সংস্কার’! যাদের বাড়িতে পঞ্জিকা ছিল না, যাদের পূর্বপ্রজন্ম পঞ্জিকা দেখবার প্রয়োজন বোধ করত না, এমন কি যাদের জীবনে পঞ্জিকার গুরুত্ব দেখা যায়নি কোনো দিন, তারাই উদ্যোগী হয় পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পঞ্জিকা সংস্কার তাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বাঙালির অখণ্ড চেতনার মধ্যে ধর্মীয়ভাবে একটি ভেদরেখা টানা। বাঙালি জীবনের প্রচলিত পঞ্জিকা সংস্কারের নামে খ্রিস্টীয় সনের এপ্রিলের চৌদ্দ তারিখের সঙ্গে সেঁটে দেয়া হয় পহেলা বৈশাখ! শুধু তাই নয়, বাংলা সন আরম্ভ হতো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এই নতুন নিয়মে রাত বারটার পর থেকে এখন বাংলা সন আরম্ভ হবে। কী অ™ভুত, কী উপনিবেশকামী মানসিকতা, কী কূটসাম্প্রদায়িকতা!! খ্রিস্টীয় সনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে লিপইয়ার থাকবে, বছরের দিবস কম-বেশি হবে, মাসগুলোও যে যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকবে আর তাকে অনুসরণ করবে বাংলা সন। বাংলা সনের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না। ইংরেজদের যে দিন চৌদ্দই এপ্রিল আমাদের সেদিন পহেলা বৈশাখ! ভাবটা এমন, এ ছাড়া বাংলা সন বা তারিখের বাঙালির জীবনে আর কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে প্রশ্ন: পহেলা বৈশাখের নামে আমরা কি প্রকারান্তরে চৌদ্দই এপ্রিলই উদ্যাপন করছি না? বাংলা সনকে কি শুধুই পহেলা বৈশাখে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি না আমরা? এ রকম অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যেই প্রতি বছর আসে পহেলা বৈশাখ। নতুন প্রজন্ম এখন জানে, পহেলা বৈশাখ দুদিনÑ বাংলাদেশে এক দিন, পশ্চিমবঙ্গে আরেক দিন। এই জানাকে সাম্প্রদায়িকতা দিয়েও বোঝে অনেকেÑ বলে, হিন্দুদের পহেলা বৈশাখ এক দিন, মুসলিমদের পহেলা বৈশাখ আরেক দিন!! কিন্তু তারা আজ জানে না, এই স্বাধীন বাংলাদেশেই কিছু কাল আগে পঞ্জিকা সংস্কারের নামে বাংলা সনের সর্বনাশ করা হয়। সন প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা মাসগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল নক্ষত্রের নামে। তাই বিশাখা নক্ষত্র সমাগমের আগেই বৈশাখ মাস গণনা আরম্ভ হতে পারে না। আমাদের পঞ্জিকা সংস্কারে নক্ষত্রের ধার ধারা হয়নি। বাংলাদেশে চৌদ্দ এপ্রিল মানেই পহেলা বৈশাখ! এ-ও সম্ভব!! লেখকঃ অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
|
| |
|
|
|